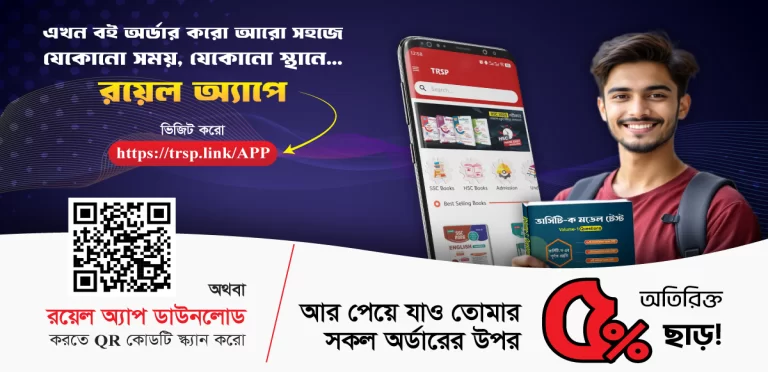অভাগীর স্বর্গ - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
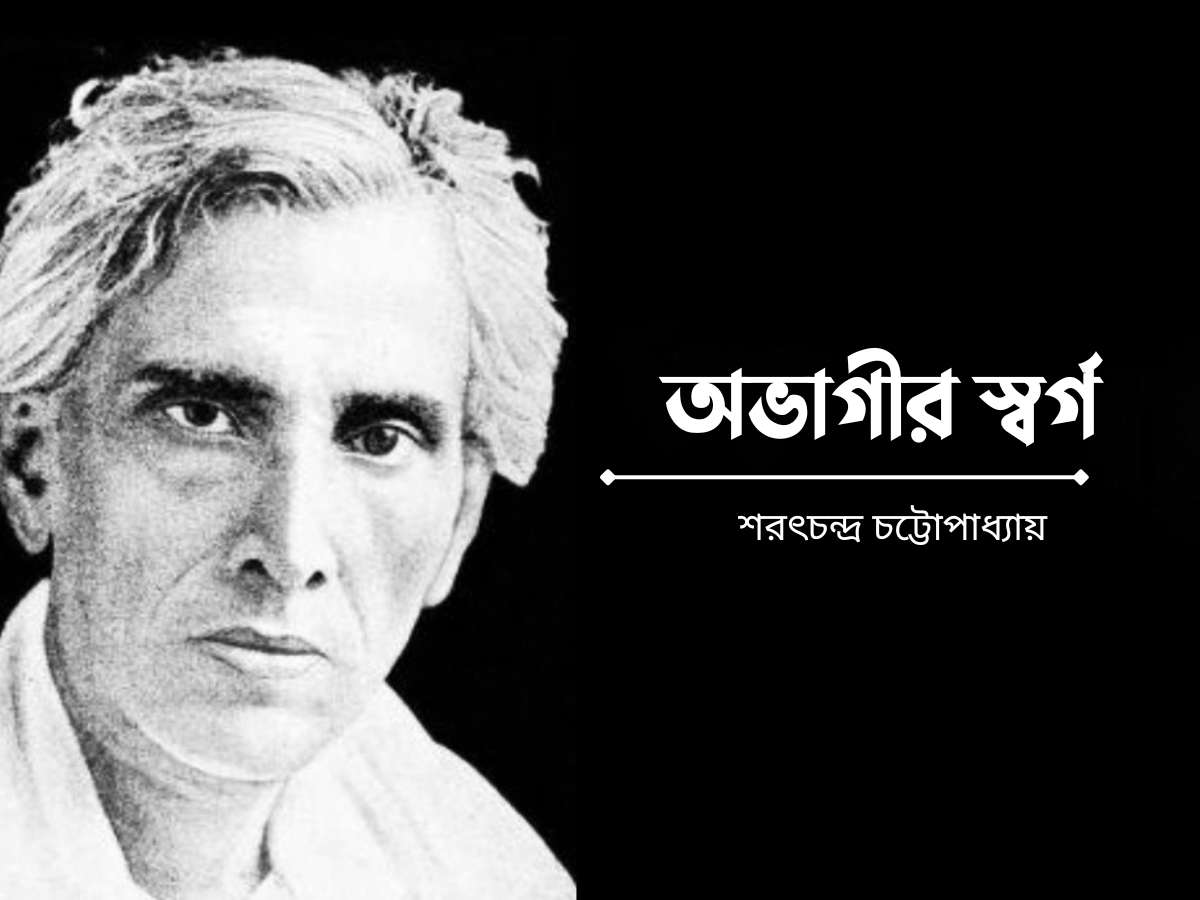
ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী
স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয়
সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলেমেয়েদের ছেলে-পুলে হইয়াছে, জামাইরা—প্রতিবেশীর
দল, চাকর-বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাঁধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধূমধামের শবযাত্রা
ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আল্তা
এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বহুমূল্য
বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া
লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার – এ যেন
বড় বাড়ির গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামীগৃহে যাত্রা
করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া
অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।
প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটী
প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর প্রাঙ্গণের
গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল
না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা – সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে
সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান।
সেখানে পূর্ব্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুকরা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধূনা প্রভৃতি উপকরণ
সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না,
তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত
উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার পরে যখন শব স্থাপিত
করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল
ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহু কণ্ঠের হরিধবনির সহিত
পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল
পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারম্বার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো – আমাকেও
আশীর্ব্বাদ করে যাও আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতে আগুন! সে
ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী পরিজন – সমস্ত সংসার
উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ – দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল
– এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধূঁয়া
নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট
একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার
কত না লতা-পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে – মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু
সিঁথায় তাঁহার সিঁদূরের রেখা, পদতল দুটি আলতায় রাঙানো। ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর
মায়ের দুই চোখ অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনেরর ছেলে তাহার আঁচলে
টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস মা, ভাত রাঁধবি নে?
মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া
কহিল, রাঁধবো’খন রে! হঠাৎ উপরে আঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ দ্যাখ
বাবা – বামুনমা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্চে!
ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া
কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস! ও ৎ ধুঁয়া! রাগ করিয়া
কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি?এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য
করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরেছে তুই কেন কেঁদে মরিস মা?
কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁস
হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এই ভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল,
এমন কি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্ত্তে চোখ মুঝিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার
চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে – চোখে ধোঁ লেগেছে বই ত নয়!
হাঁ, ধেঁ। লেগেছে বই ত না!
তুই কাঁদতেছিলে!
মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের
হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙ্গালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল –
শ্মশান সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।
সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার
মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত
হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলাকেই যেন
আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালজীবনটুকু
বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়া-
ছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না
আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙ্গালীর মা হইতে বাঁচিয়া
রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য
বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র
কাঙ্গালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।
তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া
আজ পনেরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে
আরও বছর-খানেক তাহার অভাগ্যের সহিত বুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি
দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।
কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া
আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য্য
হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?
বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন
আর ক্ষিদে নেই।
ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল,
না, ক্ষিদে নেই বই কি! কই দেখি তোর হাঁড়ি?
এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর
মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর এক জনের
মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ
করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রূগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া
বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানেই বসিয়াই তাহাকে খেলা-ধূলার
সাধ মিটাইতে হইয়াছে। এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া
কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন
আবার নেয়ে এলি? মড়া পোড়ানো কি তুই—
মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত
চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মাঠাকরুণ রথে
করে সগ্যে গেলেন।
ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল,
তোর এক কথা মা। রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়।
মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু
কাঙালী, বামুনমা রথের ওপরে বসে। তেনার রাঙা পা দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে!
সবাই দেখলে?
সব্বাই দেখলে!
কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া
বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিয়তেই সে শিশু- কাল
হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে,
তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নেই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা হলে তুইও ৎ মা সগ্যে
যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বলতেছিল, কাঙালীর মার মত সতী-লক্ষ্মী আর দুলে
পাড়ায় কেউ নেই।
কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল,
কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিল, তখন তোরে কত লোক ত নিকে
করতে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি, না। বললি, কাঙালী বাঁচলে আমার দুঃখ ঘুচবে, আবার
নিকে করতে যাবো কিসের জন্যে? হাঁ মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম? আমি হয় ত না
খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।
মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া
ধরিল। বস্তুতঃ সেদিন তাহাকে এ পরামর্শ কম লোকে দেয় নাই এবং যখন সে কিছুতেই রাজী হইল
না, তখন উৎপাত, উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া অভাগীর
চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, ক্যাঁতাটা পেতে দেব
মা, শুবি?
মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী
মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে বালিশটা পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে
বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।
কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব
কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হলে দেবে না মা!
না দিক গে – আয় তোকে রূপকথা
বলি।
আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না,
কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল তা হলে। রাজপুত্তুর কোটাল-
পুত্তুর আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া –
অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র
আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা
এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর
কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র – সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়
– নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্ত স্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিকে
বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম
নাই, বিচ্ছেদ নাই – কাঙালীর স্বপ্ন দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে,
পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।
বাহিরের বেলা শেষ হইল, সূর্য্য
অস্ত গেল, সন্ধার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে
আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকার
কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিত লাগিল।
সে সেই শ্মশান শ্মশান- যাত্রার কাহিনী। সেই রথে, সেই রাঙা পা দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে
যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি
করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের
আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি! তার আকাশ- জোড়া ধূঁয়ো ত ধূঁয়ো নয়
বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালী- চরণ, বাবা আমার! কেন মা?
তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা,
বামুনমার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।
কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল,
যাঃ – বলতে নাই।
মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও
পাইল না, তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে
পারবে না – দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস! ছেলের হাতের আগুন – রথকে যে
আসতেই হবে!
ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া
ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস নে মা, বলিস নে, আমার বড্ড ভয় করে।
মা কহিল, আর দেখ কাঙালী, তোর
বাবাকে একবার ধরে আনবি, অমনি যেন পায়ের ধূলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। অমনি
পায়ে আলতা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে – কিন্তু কে বা দেবে?তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই
আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া
ধরিল।
অভাগীর জীবন- নাট্যের শেষ
অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও
পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন
গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদা-কাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা
দিয়া তাঁহাকে একটাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিল না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত
কি আয়োজন; খল, মধু, আদার সত্ব, তুলসী পাতার রস – কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া
বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ
করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগদী-দুলের ঘরে
কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না! দিন দুই-তিন এমনি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে
আসিল, যে যাহা মুষ্টি-যোগ জানিত, হরিণের শিঙ ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া
চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ
কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোবরেজের বড়িতে
কিছু হল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এমনিই ভাল হব।
কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই
বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এমনি কি কেউ সারে?
আমি এমনি সেরে যাবো। তার চেয়ে
তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।
কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে
ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে।
উনান তাহার জ্বলে না – ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া
পড়ে; মায়ের চোখ ছল ছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা
করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া
কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল
অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল।
গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ী
দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার
ভয়ই হইল না! সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস বাবা?
কাকে মা?
এই যে রে – ও-গাঁয়ে যে উঠে
গেছে-
কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?
অভাগী চুপ করিয়া রহিল।
কাঙালী বলিল, সে আসবে কেন
মা?
অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ
ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বলবি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধূলো চায়।
সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে
সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস বাবা, বলিস, মা যাচ্চে।
একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার
পথে অমনি নাপতে বৌদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস কাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে।
আমাকে বড় ভালবাসে।
ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত।
জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখ সে এই কয়টা জিনিসের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে
যে সে সেইখানে হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।
পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন
আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে,
চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। কাঙালী
কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে – পায়ের ধূলো নেবে যে!
মা হয় ত বুঝিল, হয় ত বুঝিল
না, হয় ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল।
এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।
রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া
রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা
তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের
ধূলো। রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশন বসন দেয়
নাই, কোন খোঁজ খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া
ফেলিল। রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন কায়েতের ঘরে না জন্মে ও আমাদের দুলের
ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা – কাঙালীর হাতের আগুনের লোভে ও যেন
প্রাণটা দিলে।
অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে
বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত
বিঁধিল।
সেদিন দিনের-বেলায় কাটিল,
প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না।
কি জানি, এত ছোটজাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিম্বা অন্ধকারে পায়ে
হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বুঝা গেল রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া
সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।
কুটীর প্রাঙ্গণে একটা বেল
গাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমি- দারের দরওয়ান
কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া
লইয়া কহিল, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস?
রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল,
কাঙালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজী। বাবাকে
খামোকা তুমি মারলে কেন?
হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও
একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া
বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তার গায়ে হাত দিল না। হাঁকা-হাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া
উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয়
নাই। তাহারই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা
হুকুম দেন। কারণ অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাতে ধরিয়া
তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে। দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত মুখ নাড়িয়া
জানাইল, এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।
জমীদার স্থানীয় লোক নহেন;
গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্ত্তা। লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার
কাছে ব্যর্থ অনুনয় করিতে লাগিল, কাঙালী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারী বাড়িতে
আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয়
বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্ত্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান
না হইয়াই পারে না। হায়রে অনভিজ্ঞ! বাঙলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীকে সে চিনিত
না। সদ্যমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল,
অধর রায় সেইমাত্র সন্ধাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত
ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?
আমি কাঙালী। দরওয়ানজী আমার
বাবাকে মেরেছে।
বেশ করেচে। হারামজাদা খাজনা
দেয় নি বুঝি?
কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়,
বাবা গাছ কাটতেছিল -আমার মা মরেচে -, বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।
সকাল-বেলা এই কান্না-কাটিরে
অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া
ফেলিল না কি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নিচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস রে, এখানে
একটু গোবর- জল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?
কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া
দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।
অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ায়
কাঠ কি হবে শুনি?
কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে
আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে
শুনেছে যে! মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্ত্তে
স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।
অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি
ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন গে। পারবি?
কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব।
তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসাটি বিন্দির পিসি
একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।
অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত
করিয়া কহিলেন, না ত মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ
কুড়ুল ঠেকাতে যায় – পাজি, হতভাগা, নচ্ছার!
কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের
উঠানের গাছ বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ!
হাতে পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে
গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত!
পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল,
এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্মচারীই পারে।
কাঙালী ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া
দাঁড়াইল, তার পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা
ভাবিয়াই পাইল না। গোমস্তার নির্বিকার চিত্তে দাগ পর্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি তাহার
জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকী পড়েছে কি না। থাকে ত জাল-টাল
কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়,-হারামজাদা পালাতে পারে।
মুখুয্যে বাড়িতে শ্রাদ্ধের
দিন – মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকী। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে।
বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতে- ছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে
দাঁড়াইয়া কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা মরে গেছে।
তুই কে?কি চাস তুই?
আমি কাঙালী। মা বলে গেছে তেনাকে
আগুন দিতে।
তা দিগে না।
কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই
মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। এই বলিয়া
সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।
মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত
হইয়া কহিলেন, শোন আবদার। আমারই কত কাঠের দরকার – কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে
কিছু হবে না – এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। ভট্টাচার্য্য
মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায়
রে-যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে।
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড়ছেলে
ব্যস্ত সমস্ত ভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন,
দেখছেন ভটচাযমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর
কোথায় চলিয়া গেলেন।
কাঙালী আর প্রার্থনা করিল
না। এই ঘন্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল, নিঃশব্দে
ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।
নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে
শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙ্গালীর হাতে একটা খড়ের আটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত
ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে সকলে মিলিয়ে মাটি চাপা দিয়া
কাঙালির মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল। সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া
খড়ের আটি হইতে যে স্বল্প ধূঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি
পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী উর্দ্ধদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।