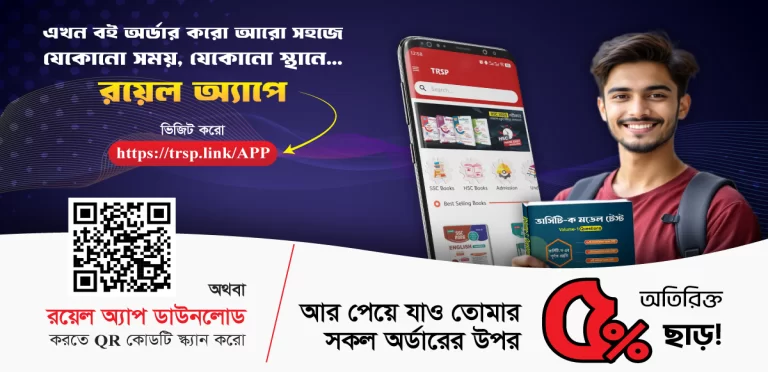পর্যায় সারণিঃ মেন্ডেলিফ থেকে নীলস বোর
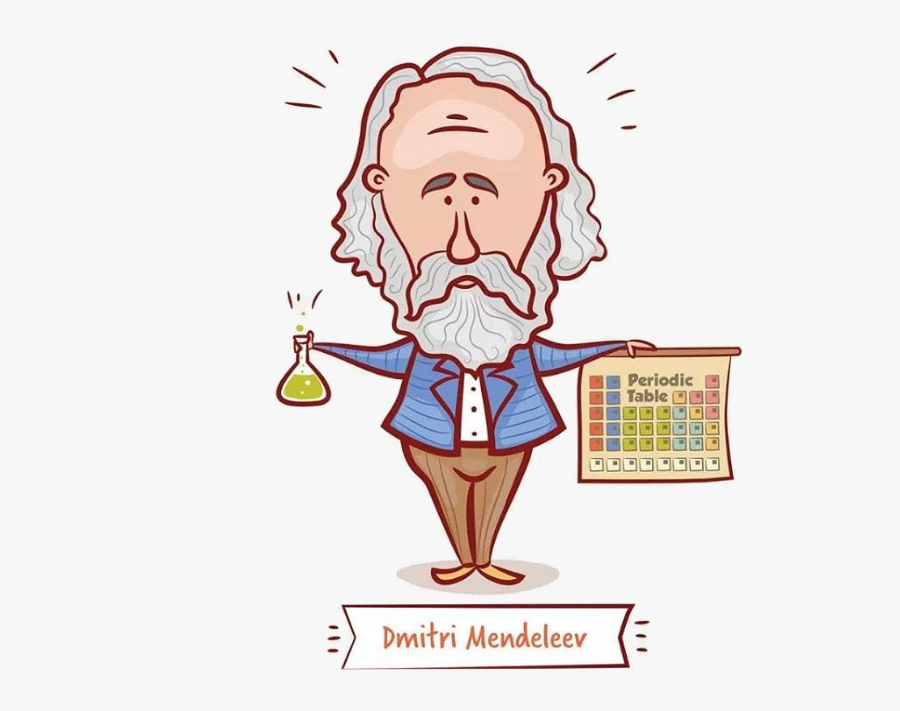
দিমিত্রি মেন্ডেলিফ পারমাণবিক সংখ্যার ক্রমানুসারে প্রায় একই ধরনের ধর্মবিশিষ্ট মৌলসমূহকে একই শ্রেণীভুক্ত করে, আবিষ্কৃত সব মৌলকে স্থান দিয়ে মৌলসমূহের যে সারণি তৈরি করা হয়, তাকে মৌলের পর্যায় সারণি বলা হয়।
মানুষ প্রাচীনকাল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে পদার্থ এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে যে সকল ধারণা অর্জন করেছিল পর্যায় সারণি হচ্ছে তার একটি সম্মিলিত রূপ। পর্যায় সারণি একজন বিজ্ঞানীর একদিনের পরিশ্রমের ফলে তৈরি হয়নি। অনেক বিজ্ঞানীর অনেক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজকের এই আধুনিক পর্যায় সারণি তৈরি হয়েছে।

1789 সালে ল্যাভয়সিয়ে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ফসফরাস, মার্কারি, জিংক এবং সালফার ইত্যাদি মৌলিক পদার্থসমূহকে ধাতু ও অধাতু এই দুই ভাগে ভাগ করেন। ল্যাভয়সিয়ের সময় থেকেই মৌলগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় যেন একই ধরনের মৌলিক পদার্থগুলো একটি নির্দিষ্ট ভাগে থাকে। ল্যাভয়সিয়ে তাঁর সময়ে 33 টি মৌল নিয়ে ছক তৈরি করেন।

1829 সালে বিজ্ঞানী ডোবেরাইনার লক্ষ্য করেন তিনটি করে মৌলিক পদার্থ একই রকমের ধর্ম প্রদর্শন করে।তিনি প্রথমে পারমাণবিক ভর অনুসারে তিনটি করে মৌল সাজান।এরপর তিনি লক্ষ্য করেন দ্বিতীয় মৌলের পারমাণবিক ভর প্রথম ও তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভরের যোগফলের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি, একে ডোবেরাইনারের ত্রয়ীসূত্র বলে। বিজ্ঞানী ডোবেরাইনার লিথিয়াম (Li), সোডিয়াম (Na) ও পটাশিয়াম (K) কে প্রথম ত্রয়ী মৌল হিসেবে চিহ্নিত করেন। (এই তিনটি মৌলই ক্ষারধাতু; এমনকি এদের ধর্মগুলো প্রায় কাছাকাছি।)



1864 সাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলসমূহের জন্য নিউল্যান্ড অষ্টক সূত্র নামে একটি সূত্র প্রদান করে।

অষ্টক সূত্র:
মৌলসমূহকে যদি পারমাণবিক ভরের ছোট থেকে বড় অনুযায়ী সাজানো যায় তবে যেকোনো একটি মৌলের ধর্ম তার অষ্টম মৌলের ধর্মের সাথে মিলে যায়।

এখানে, Li এর সাথে এর অষ্টম মৌল Na এর ধর্মের মিল রয়েছে (তারা উভয়ই ক্ষারধাতু),
অনুরূপভাবে, Be এর সাথে এর অষ্টম মৌল Mg এর মিল রয়েছে এবং B এর সাথে এর অষ্টম মৌল Al এর ধর্মের মিল দেখা যায়।
1869 সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফ সকল মৌলের ধর্ম পর্যালোচনা করে একটি পর্যায় সূত্র প্রদান করেন। সূত্রটি হলো:
“মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়”।

এ সূত্র অনুসারে তিনি তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত 63টি মৌলকে 12টি আনুভূমিক সারি আর 8টি খাড়া কলামের একটি ছকে পারমাণবিক ভর বৃদ্ধি অনুসারে সাজিয়ে দেখান যে, একই কলাম বরাবর সকল মৌলগুলোর ধর্ম একই রকমের এবং একটি সারির প্রথম মৌল থেকে শেষ মৌল পর্যন্ত মৌলগুলোর ধর্মের পরিবর্তন ঘটে।
এই ছকের নাম দেওয়া হয় পর্যায় সারণি (Periodic Table)|

পরবর্তীতে আবিষ্কৃত মৌলসমূহকে মেন্ডেলিফের সূত্রানুসারে সাজাতে গিয়ে বিভিন্ন অসংজ্ঞতির উদ্ভব হয়। যেমন, আর্গনের পারমাণবিক ভর 40 এবং পটাশিয়ামের পারমাণবিক ভর 39 হওয়া সত্ত্বেও একই গ্রুপে ধর্মের মিল রাখতে আর্গনকে পটাশিয়ামের আগে বসাতে হয়েছিল। এরকম আরও অনেক মৌলের ক্ষেত্রে দেখা যায় পারমাণবিক ভর বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে কোনো কোনো মৌলের আগে পর্যায় সারণিতে বসানো হয়েছিল। এটি ছিল এই পর্যায় সারণির ত্রুটি। এরকম আরও অনেক ত্রুটি মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মেন্ডেলিফের এই পর্যায় সারণিই আধুনিক পর্যায় সারণির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল; তাই মেন্ডেলিফকে পর্যায় সারণির জনক বলা হয়।

1913 সালে মোসলে পারমাণবিক ভরের পরিবর্তে পারমাণবিকসংখ্যা অনুযায়ী মৌলগুলোকে পর্যায় সারণিতে সাজানোর প্রস্তাব দেন। মোসলের প্রস্তাবনা অনুসারে মৌলসমূহকে পর্যায় সারণিতে তাদের পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজানোর পর মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে উদ্ভব হওয়া ত্রুটিগুলো সংশোধিত হয়।

পরবর্তীতে বিজ্ঞানী নীলস বোর ইলেকট্রন বিন্যাসকে পর্যায়সারণি রভিত্তি হিসেবে ধরে বিস্তৃত পর্যায় আকারের একটি পর্যায় সারণি তৈরি করেন। এটি দীর্ঘাকার পর্যায় সারণি বা বোরের পর্যায় সারণি নামে পরিচিত।

বর্তমানে এ পর্যায় সারণিতে 7টি পর্যায় এবং 18টি শ্রেণি বা গ্রুপে IUPAC স্বীকৃত 118টি মৌল রয়েছে। দীর্ঘ পর্যায়ে 10টি করে d-ব্লক মৌল পর্যায় সারণির মধ্যভাগে থাকে। প্রতি পর্যায়ের শেষ প্রান্তে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোর অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ল্যান্থানাইড ও অ্যাক্টিনাইড মৌলগুলোকে পৃথক দুই সিরিজ হিসেবে এ সারণির ষষ্ঠ এবং সপ্তম পর্যায়ের তৃতীয় গ্রুপে রাখা হয়েছে। এটিই হলো আধুনিক পর্যায় সারণি।

তথ্য উৎস্য:
দি রয়েল সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত
Periodic Table (Heart Of Chemistry) Level SSC
Periodic Table (Heart Of Chemistry) Level HSC
বইটির কিছু অংশ পড়ে দেখতে ক্লিক করুন Periodic Table HSC Periodic Table SSC
লেখাঃ Jahid Mahmud
BSc. BUET
jahidmahmud4@gmail.com